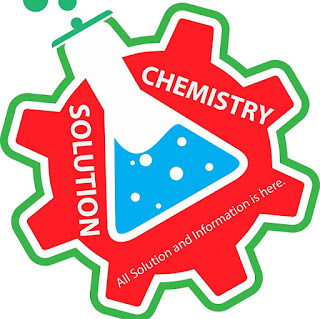মূলত পোলারায়ন এর জন্যই PbCl2 এর বর্ণ সাদা হলেও PbI2 এর বর্ণ উজ্জ্বল সোনালি হলুদ হয়।
আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় , যখন কোন ক্যাটায়ন একটি অ্যানায়নের খুব নিকটে আসে তখন ক্যাটায়নের সামগ্রিক ধনাত্নক চার্জ অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। একই সাথে ক্যাটায়নটি অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসকে বিকর্ষণ করে।আকর্ষণ বিকর্ষণ এর নীট ক্রিয়ায় অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের দিকে সরে আসে। এ ঘটনাকে ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের বিকৃতি বা পোলারায়ন বলে ।।
পোলারায়ন পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌগের প্রকৃতি আদর্শ আয়নিক বন্ধনের প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে সমযোজী প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়।
এ বিষয়ট "ফাজানের সূত্র " দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। আয়নিক যৌগের আয়নিক বন্ধনের এরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফাজান 1923 সালে কিছু শর্তের প্রস্তাব করেন। এ শর্তগুলি হলো-
- ক্যাটায়নের আকার যতো ছোট এবং অ্যানায়নের আকার যতো বড় হয়।
- ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জের পরিমাণ যতো বেশি হয়।
- ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে d ও f অরবিটালে ইলেকট্রনের উপস্থিতি।
১ম শর্ত হতে বলা যায় একই ক্যাটায়ন দ্বারা গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগে অ্যানায়নের আকার ভিন্ন হলে যৌগের মধ্যে পোলারায়নের মাত্রাও ভিন্ন হয়। যৌগে অ্যানায়নের আকার বড় হলে যৌগের পোলারায়ন মাত্রা বেড়ে যায়। এ পোলারায়ন আরো বেড়ে যায় যদি যৌগটি আলোকরশ্মি শোষণ করে। সাধারণত অতিবেগুনি রশ্মি, X-Ray এর ন্যায় উচ্চ কম্পাঙ্কের রশ্মি শোষণ করলে যৌগের মধ্যে পোলারায়ন মাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি দৃশ্যমান আলোকরশ্মি শোষণ করলেও পোলারায়ন সহজ হয়। দৃশ্যমান আলো সাতটি বিভিন্ন কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলোর সমষ্টি। দৃশ্যমান আলো যৌগের ওপর আপতিত হলে বিভিন্ন কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মির মধ্যে কয়েকটি বর্ণের আলোকরশ্মি যৌগ কর্তৃক শোষিত হয়ে পোলারায়ন ঘটায়। অবশিষ্ট আলোক রশ্মিগুলো প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোক রশ্মিগুলো মিলিত হলে বর্ণ নির্ধারিত হয়। বিকিরিত রশ্মিগুলো মিলিত হয়ে যে বর্ণের সৃষ্টি করে যৌগটি সে বর্ণের হয়।
PbI2 ও PbCl2 যৌগে ক্যাটায়ন একই আর সেটি হচ্ছে Pb2+
PbI2 যৌগে I- এর আকার বড় হওয়ায় দৃশ্যমান আলোকরশ্মি যৌগটির ওপর পড়লে কয়েকটি বর্ণের আলোকরশ্মি PbI2 দ্বারা শোষিত হয় এবং যৌগের অণুতে পোলারায়ন ঘটায়। অবশিষ্ট আলোকরশ্মি যৌগটি দ্বারা প্রতিফলিত হয়। বিকিরিত বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মি মিলিত হয়ে উজ্জ্বল সোনালি হলুদ বর্ণের সৃষ্টি করে।
PbCl2 যৌগের Cl- আয়নের আকার I- আয়ন অপেক্ষা যথেষ্ট ছোট হওয়ায় দৃশ্যমান আলোর সাতটি বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি PbCl2 অণুতে পোলারায়ন ঘটাতে পারে না। এ দৃশ্যমান আলো PbCl2 যৌগের বন্ধনের উপর কোনোভাবে পোলারায়ন না ঘটিয়ে রশ্মির সামান্য অংশ শোষিত হয়। অবশিষ্ট সাতটি বর্ণের আলোকরশ্মি মিলিত বর্ণ হলো সাদা ।
এ কারণে PbI2 যৌগের বর্ণ উজ্জ্বল সোনালি হলুদ হলেও PbCl2 যৌগের বর্ণ সাদা হয়।।
PbI2 যৌগটির বন্ধন পূর্ণ আয়নিক (ionic) নয়। কিছুটা সমযোজী (Covalent) বন্ধন ধর্মও বিদ্যমান। সুতরাং, বর্ণহীন আয়ন I(-) এবং Pb(2+) যুক্ত হয়ে একটি নতুন যৌগ গঠন করে যার বর্ণ হলুদ।
এমন অনেক উদাহরণ আছে যারা বর্ণহীন আয়ন (-) এবং (+) যুক্ত হয়ে একটি নতুন বর্ণযুক্ত যৌগ গঠন করে। যেমনঃ
Hg(2+) + 2I(-) --> HgI2 (colorless --> very bright red/orange)
Pb(2+) + S(2-) --> PbS (colorless --> black)
Cd(2+) + S(2-) --> CdS (colorless --> bright yellow)
Cd(2+) + Se(2-) --> CdSe (colorless --> red)
কারন এ ধরনের যৌগগুলো যাদের বর্ণ আছে এদের সমযোজী (Covalent) বন্ধন থাকার কারনে এরা বড় ইলেকট্রন অর্বিটাল গঠন করে এবং এসব অর্বিটালের ion গুলো অনুর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারনতঃ এ ধরনের বড় ইলেকট্রন অর্বিটাল দীর্ঘ তরঙ্গর আলোর বর্ণালির সাথে মিথষ্ক্রিয়া ঘটানোর সামর্থ্য রাখে এবং দৃশ্যমান বর্ণালিগুলোতে প্রবেশ করে। এর ফলে যৌগগুলোর ইলেকট্রন অর্বিটাল গঠন অনুযায়ী ion গুলো যার যার নির্দিষ্ট দৃশ্যমান বর্ণালিগুলোতে প্রবেশ করে শোষিত হয় এবং নির্দিষ্ট বর্ণ বিকিরন করে। সাধারনতঃ ছোট ion গুলো UV range এ শোষিত হয়।
PbI2 এর ion সমূহ শোষিত হয় বর্ণালির ৫৭৫ ন্যানোমিটার হতে ৫৮৫ ন্যানোমিটার বিস্তারের মধ্যে। বর্ণালির ৫৭৫-৫৮৫ ন্যানোমিটার উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ প্রদর্শন করে থাকে।